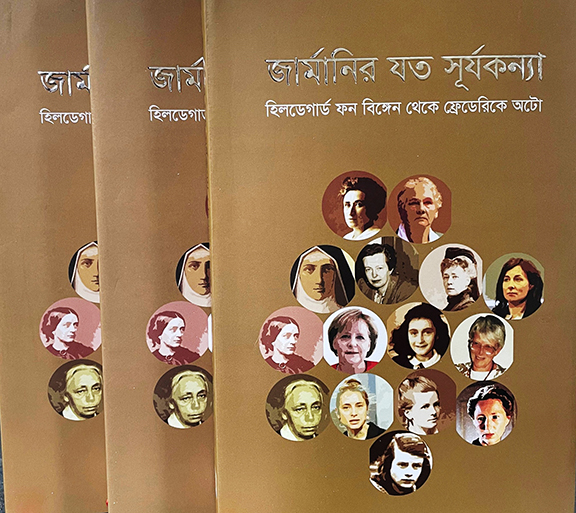(পূর্ব প্রকাশের পর)
আবদুল্লাহ আল-হারুন, জার্মানি থেকে: ২০১০ সালের অক্টোবর মাসে এক শীতের দুপুরে দুই নম্বর গ্রামে জনের নেতৃত্বে গীর্জায় একটি বিশেষ প্রার্থনা সভায় যোগ দেন প্রাদেশিক সরকারের প্রধানমন্ত্রী ও মন্ত্রিপরিষদের অনেক সদস্য, নয়ে-ইজেনবুর্গসহ আশেপশের ৪-৫টি শহরের মেয়র, জাতীয় ও স্থানীয় রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ, বার্লিন থেকে কেন্দ্রিয় সরকারের শিল্প ও অর্থমন্ত্রী, জার্মানির নামকরা কিছু টাইকুন-ব্যবসায়ী (যারা প্রকল্পটিতে সিংহভাগ লগ্নি করছে)। ঐদিন গীর্জার সামনের মাঠে বিরাট প্যান্ডেল বাঁধা হয়েছিল। পাশেই প্রধান মন্ত্রী সম্মিলিত বিশেষ অতিথিদের সাথে উদ্বোধনী বেদীতে কার্নিস দিয়ে সিমেন্ট গেঁথে তিন হাজার কোটি দামের প্রজেক্টটির শুভ (!)সূচনা করলেন। বেদীতে তার নাম, তারিখ ও প্রকল্পটির নাম খোদাই করা। তার পাশে একটি বিরাট বোর্ডে প্রকল্পটির চিত্র ও বর্ণনা। স্থানীয় যারা বাড়িঘর ছেড়ে অফেনবুর্গে হিজরত করেছেন, তাদের ৩০-৩৫ জন উপস্থিত ছিলেন। কারও মুখে হাসি, কারও বিরস বদন। মার্টিন-শার্লট (পাশে ওদের বাড়িটিই গীর্জা ছাড়া একমাত্র অবশিষ্ট!) আসেনি। মেলিও আসেনি। মন্ত্রীর রাজমিস্ত্রির কাজটি সম্পন্ন হবার পরই রাজসূয় যজ্ঞ শুরু হলো। বিরাট খাওয়া দাওয়া এবং শতাধিক প্রকারের নানা ধরনের বোতলে অ্যালকোহলের বহ্নুৎসব। জন আমাকে বলল, এখানে তোমার আমার কিছু করার নেইা। তুমি তো মদ বহু আগেই ছেড়ে দিয়েছ। আমি সাধারণ লাল মদ (ধর্মীয় অনুষ্ঠানের সময়) এবং মাঝে মাঝে একাধটু বিয়ার খাই। হুইস্কি-স্যাম্পেনে আমার কোনই আগ্রহ নেই। চল, মার্টিনদের দেখে আসি।
মার্টিনদের বাড়ি দোতালা। একতালার পেছনের বারান্দায় স্বামী-স্ত্রী মুখ শুকনো করে বসে আছে। কথাবার্তা জমল না। জমার কথাও নয়। শার্লট একবার জিজ্ঞেস করল, কফি খাবো কিনা। আমরা দুজনেই একসাথে ধন্যবাদ জানিয়ে না বললাম। আসার সময় মার্টিন বলল, সামনের ক্রিসমাসের উৎসবে আমি যেন অবশ্যই আসি এবং সেদিন দুপুর ও রাতের খাবারের নিমন্ত্রণও অগ্রিম দিয়ে রাখল। জন বলল, ‘আবদুল্লাহ অবশ্যই আসবে তবে রাত বা দুপুরে ও একবেলা আমার ওখানে খাবে। এবং রাতে আমার বাসায় থাকবে। তোমাদের এখানে দু‘বেলা খাওয়া ও রাত্রিবাসের কষ্ট দেয়াটা ঠিক হবে না।’ ‘আগে ডিসেম্বর মাস তো আসুক। তখন দেখা যাবে কোথায় যাই, কোথায় থাকি!’, আমি। বললাম। অনুষ্ঠানের সামিয়ানার জায়গার পাশ দিয়ে যাবার সময় মাতাল অতিথিদের হৈচৈ এবং উচ্চস্বরে বেসুরো কোরাস গান শোনা গেল। অ্যালকোহল পুরাপুরি অধিকার করে ফেলেছে ওদের। করবেই বা না কেন্? সবারই স্বপ্ন, সামনে হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ টাকা!
কয়েকবার কড়া নাড়ার পরও মেলি দরজা খুলছে না দেখে, জন চিন্তিত হয়ে পড়ল। ‘কয়েকদিন ধরেই মেলি উদাসীন এবং বাড়ির বাইরে বেরোয় না। গত রবিবার গীর্জাতেও আসেনি। আমি ওকে গতরাতে আজকের অনুষ্ঠানে আসার জন্য বলতে এসেছিলাম। ওর টেলিফোন অনেক দিন থেকেই খারাপ। কিন্ত ও দরজা না খুলে ভেতর থেকেই বলল, অত্যন্ত দুঃখিত। শরীর খারাপ। বিছানায় শুয়ে আছি। আগামীকাল আসতে পারব না।্’ জনের দীর্ঘ বক্তব্যে বুঝতে পারলাম, এর মধ্যে ২-৩বার মেলিকে টেলিফোন করে আমি কেন তাকে পাইনি। বিষ্মিত হলাম, রিং তো হয়েছিল! ও ধরল না কেন? এখন জানলাম, টেলিফোন খারাপ। আমি বললাম, ‘ও যখন দেখা করতে চায় না, কথা বলতে চায় না, আজ বরং আমরা চলেই যাই। তুমি আগামীকাল এসে আবার একবার চেষ্টা করো ওর সাথে কথা বলতে। আমি দেখি সামনের শনিবার বা রবিবার আসতে পারি কিনা।’ জন বুঝতে পারল, আমি মেলিকে বর্তমান অবস্থায় বিরক্ত করতে চাই না। দুজনে ফিরে এলাম।
মেলির সাথে আমার আর দেখা হয়নি। পরের শনিবার-রবিবার আমার কোথায় যেন আগে থেকেই একটা কর্মসুচি ছিল। কয়েক সপ্তাহ পরে জন এল আমার বাসায়। ওর কাছেই শুনলাম, রেবেকা স্বামীসহ আমেরিকা থেকে এসে ১০-১২দিন ছিল। অনেক বুঝিয়ে ও জেদ করে মেলিকে আমেরিকা নিয়ে গেছে। মেলি নাকি শেষের দু‘তিন মাস মোটামুটি নির্বাকই থাকত। নিজের থেকে কিছুই বলত না। ওর মনের কোনে কোথায় যেন একটা আশা ছিল, হয়ত ওর বাড়িটা থেকে যাবে। কারণ প্রকল্পে তার বাড়িটা একটি প্রাকৃতিক জঙ্গল হিসেবে ধরা হয়েছিল। পুরোটা বন হয়েই থাকবে ও বহুবার প্রকল্পের লোকজনদের অনুরোধ করেছে, তার জায়গাটা যখন সংরক্ষিত বনের ভেতরেই, তার বাড়িটাকেও তাহলে ওর মধ্যেই যেভাবে আছে সেভাবেই রাখা হোক। কিন্ত তথাকথিত ‘জার্মান পারফেক্সনিস্ট’রা এটা মেনে নেয়নি। যাবার আগে মেয়েকে সাথে নিয়ে এসে ঘরের চাবি, যীশু খৃষ্টের কয়েকটি ছবি, পরিবারের বাইবেল এবং তার কাছে সঞ্চিত নগদ বিশ হাজার ইউরো জনকে দিয়ে যায়। ক্ষতিপূরণের টাকাও সে গীর্জাকে দান করেছে। এ সম্পর্কে জনকে পাওয়ার অব অ্যাটর্নি করে সে প্রকল্প-অধিকর্তাকে তার লিখিত সম্মতি জানিয়ে গেছে। ঘরের আসবাবপত্র রেডক্রসকে দিয়ে অনুরোধ করেছে, সামর্থ্যহীন যাদের এগুলো কাজে আসবে, তাদের দিতে। আবদুল্লাহর সাথে দেখা করবে না, এটা জিজ্ঞেস করলে মেলি বলেছিল, না এখন দেখা করবে না। তবে ও তো ফিরে আসবেই, তখন দেখা হবে। ‘আবদুল্লাহর সাথে আমার একদিন দেখা হবেই।’ বিড় বিড় করে এ বাক্যটি নাকি সে কয়েকবার বলেছিল। এ কথায় রেবেকাও নাকি আশ্চর্য হয়েছিল। জনের কাছেও এটা বিস্ময়কর মনে হয়েছিল। কথাটির অর্থ সে বুঝতে পারেনি।
আমিও এর অর্ন্তর্নিহিত সত্যটি তখন বুঝিনি। পরে যথারীতি মেলিকে আমি ভুলে যাই। এরকম অনেক পরিচয় ও -ঘটনা আমার জীবনে অহর্নিশি ঘটেছে। কত কিছু শুনেছি। কতজনের সাথে দেখা! অধিকাংশই বিস্মৃতির অতল তলে তলিয়ে গেছে। তবে আমেরিকা চলে যাবার আগে আমার সাথে দেখা করলো না বা আমাকে (মাত্র ১৫ কিলোমিটার দূরত্বে) একটা টেলিফোনও করল না, এর জন্য পরে অনেকদিন পীড়া অনুভব করেছি।
যমজ বোন অট্টালিকা দু’টির উপান্তেই এ শহরের জঙ্গলের শুরু। জার্মানিতে প্রায় শহরেই অন্তত একটি দিকে ঘন জঙ্গল আছে। দু’দিক, তিনদিক এবং চারদিকেও আছে। এ শহরের মাঝখানে পার্কে বেশ ঝোপঝাড়। শহরের বাইরে যে বনের শুরু তা একবারে অফেনবুর্গ-বিটবুর্র্গ রাস্তায় গিয়ে শেষ হয়েছে। জঙ্গল থেকে এই রাস্তায় উঠে এলে বামদিকে দু’কিলোমিটার পরে বিটবুর্গ-১ যেখানে একদা মেলির বাড়ি ছিল। তারপর বিটবুর্গ-২,৩ ও ৪ হয়ে অফেনবুর্গ। ডান দিকে ৮-৯ কিলোমিটার পরে ডিবুর্গ। এ রাস্তাটি বিটুমিনের, প্রশস্ত, গাড়ী চলাচলের জন্য। দু’পাশে ফুটপাথ আছে।
দু’কিলোমিটার পরে হাতের ডান দিকে একটা সরু রাস্তা, পাঁচশ গজ পরেই ছিলা মেলির বাড়ি। তখনি পুরো এলাকাটি ছিল ঘন জঙ্গল। রাস্তাটি দিয়ে মেলির হাফট্রাক কোনমতে চলত। ট্রাক্টর ছিল এক সময়ে। তখন নিয়মিত কিছু গাছপালা কেটে ও ঝোপঝাড় ছেটে রাস্তাটি বড় করা হতো। স্বামী মারা যাবার পরেই খেতিবারি শেষ। ট্রাক্টরটি বেঁচে দিয়েছিল মেলি। অতিথি যারা গাড়িতে আসত, তারা গাড়ি বড় রাস্তাতেই রেখে দিত। মেলিদের বাড়ির সামনে পেছনে এক বিঘার মত সবজি ও ফলের বাগান। যা এক কাঁধ উঁচু কাঁটা মেহদির বেড়া দিয়ে ঘেরা ছিল। পেছনে বেড়ার পরেই ঘন প্রাকৃতিক জঙ্গল সরকার কর্তৃক সংরক্ষিত। ওখানে বেশ কিছু পরিমাণ বন এক সময়ে ছিল মেলিদের সম্পত্তি। বাবা এবং স্বামী ওখানে চাষবাস করত। স্বামী মারা যাবার পর মেলি বনবিভাগকে ওদের জঙ্গল বিক্রি দিয়েছিল। তার একার পক্ষে জঙ্গল দেখাশোনা সম্ভব ছিল না। আমি ওর বাড়িতে গেলে দু’জনে বাড়ির পেছনে গিয়ে ওখানে কাঠের বেঞ্চে বসে গল্পগুজব করতাম। ওর দাদা নাকি ওদের জঙ্গল থেকে বার্চ গাছের এই বেঞ্চ দুটি ও টেবিলটি নিজের হাতে বানিয়েছিল। প্রায়ই দেখতাম, মেলি মেহেদির বেড়ার পাশে দাঁড়িয়ে জঙ্গলটির দিকে অপলক চোখে তাকিয়ে থাকত। কি দেখত?
লিফট দিয়ে নিচে নেমে যখন আমি বাসা থেকে বেরিয়ে এলাম, সকাল সাড়ে ছ’টা বেজে গেছে। সুর্যের তেজের প্রখরতায় মনে হয় সকাল দশটা-এগারোটা। রাস্তায় গাড়ি চলাচল তেমন শুরু হয়নি। আশেপাশে পথচারী শুধু একা আমিই। বাড়ির সামনের উঠানে সরিবদ্ধ গাড়ি। মালিকরা এখনও ঘুমিয়ে। রাস্তায় বেরোবার পর পাশাপাশি আরেকটা আবাসিক এলাকা দেখা যায়। ওখানে দু’একটি শিশুকে দেখা গেল, মায়ের হাত ধরে, কাঁধে স্কুলব্যাগ নিয়ে কিন্ডারগার্টেনে যাচ্ছে। কল কল করে কথা বলছে। দু’একজনের মুখে এখনও ঘুমের ছাপ, বিরক্তি। স্কুলে না যেতে চাওয়াটা আন্তর্জাতিক।
একটা আন্ডার ব্রিজ দিয়ে জঙ্গলে ঢুকলাম। উপরের রাস্তাটি হাইওয়ে। বেশ কিছু গাড়ি চলছে। জঙ্গলে রৌদ্রের মুখে ঘোমটার মত পাতলা অন্ধকার। ছোট দু’পেয়ে রাস্তা। ছোট ছেট পাথর ফেলা। ঢুকতেই গাড়ি চলাচলের নিষিদ্ধ সাইনবোর্ডটা হুঁশিয়ারীর ভঙ্গিতে বুক টান করে দাঁড়িয়ে আছে। হাঁটা ছাড়া সাইকেল এবং বাচ্চাদের প্যারাম্বুলেটর মায়েরা ঠেলে নিয়ে যেতে পানে। গাছেরা সামান্য দূরত্বে গায়ে গায়ে লাগিয়ে। এটাও প্রাকৃতিক বন। কর্তৃপক্ষের অনুমতি ছাড়া গাছ কাঁটা বা কোন ক্ষতি করা কবীরা গুনাহ। রাস্তার বাইরে পা রাখারও অনুমতি নেই। কিছু বিরল প্রজাতির গুল্ম-লতাপাতা আছে, যেগুলি পদচাপে আহত হয়! জার্মানরা অত্যন্ত বাধ্য ও আইনানুগ নাগরিক। একা চলছে, কয়েক কিলোমিটারের মধ্যে কেউ নেই, তারপরও আইনমত পা ফেলে চলছে! আমি বনের ভেতরে ঢুকে বাঁ দিকে মোড় নিলাম। এটাই দশ কিলোমিটার দুরে অফেনবুর্গ-বিটবুর্গ সড়কে আমাকে নিয়ে যাবে।
বার্চ, ওক এবং লিন্ডে এরা হলো বৃক্ষদের মধ্যে উচ্চশ্রেণির। এদের গড় বয়স ৩-৪শ’বছর। আকারেও বেশ বড় হয়। লিন্ডেকে দেখতে আমাদের বট গাছের মত। শুধু ডাল থেকে কোন শেকড় নামে না। অসংখ্য জানা অজানা লতাপাতার ঝোপঝাড়। অনেক বৃক্ষবিশেষজ্ঞও দেখেছি, অর্ধেক লতাপাতারই নাম জানে না। আমি সর্বমোট ১০-১২টি অনেক কষ্টে বলতে পারি। কিছু ভুলও হয়। বইতে পড়েছি, জার্মানির বনে সাধারনতঃ তিনশ’ রকমের লতাপাতা আছে! নাম জানার দরকারটি কি? আমি তো আর বৈদ্য নই। কারণ এসবের মধ্যে ওষধিই বেশি। অনেক জার্মানই সাধারন অসুখ বিসুখে ডাক্তারের কাছে যাবার আগে জঙ্গলে এসব শেকড়বাকড় খুঁজে প্রথমে তাই দিয়ে রোগটি সারানোর চেষ্টা নেন। তবে যে সব ঝোপঝাড় সবাইকে কৌতূহুলি করে তোলে, তা হল বিভিন্ন ফলমুলের। সামান্য কয়েকটার স্বাদ তেঁতুল জাতীয় হলেও অধিকাংশই অসম্ভব মিষ্টি। বেরি জাতীয় (যেমন স্ট্রবেরি) গোটা গোটা গোলগাল ফলই হবে ২০-২৫ ধরনের। সাইজ আমাদের জাম, জামরুল, কুল, ডুমুর এসবের মত। কিছুদুর পর পরই এইসব ফলেরা ইশারা করে ডাকে। অবশ্য এ ডাকাডাকি শুধুই গ্রীস্মকালে।
একটা চড়ুই পাখী লাফালাফি করছে আর পোকামাকড় খুঁজছে। কাঠবেড়ালী একটা সুড়ুৎ করে রাস্তার এ পাশ থেকে দৌড়ে ওপাশে চলে গেল! কাঠঠোকড়ার ঠক ঠক, ঘুঘু পাখির মত কি একটা পাখি যেন মাঝে মাঝেই ঘুউ ঘুউ করে ডাকছে। বহুদিন পর এই জঙ্গলের ভেতর দিয়ে বিটবুর্গের দিকে যাচ্ছি। শেষ কখন গিয়েছিলাম? আশ্চর্য হয়ে গেলাম, এই ভেবে যে ২০১০ সালে বিটবুর্গের শিল্প এলাকা উদ্বোধনের পর, এখন ২০১৭, গত সাত বছর ওদিকে যাইনি। জন মাঝে মাঝে ফোন করে। ৩-৪ মিনিট কথা হয়। তার কাছে প্রকল্পের অগ্রগতির খবর পাই। স্থানীয় পত্রপত্রিকাতেও খবর থাকে। ৩-৪ বার স্বল্প সময়ের জন্য আমার বাসাতেও এসেছিল। বুঝতে পারতাম সে গীর্জার স্থানান্তর নিয়ে অস্থিরতায় ভুগছে। অবার বিস্মিত হলাম ভেবে, গত সাত বছরে একবারও তার সাথে আমি মেলিকে নিয়ে কোন কথা জিজ্ঞেস করিনি বা সেও বলেনি। মানুষ এক বিচিত্র জীব। কত তাড়াড়াড়ি কত সহজে সে অনেক কিছুই ভুলে যায়! কত স্মৃতি কোনদিনই আর তার মনে দোলা দেয় না। গত চল্লিশ বছরের প্রবাসী জীবনে আমার কি নিজের জন্মভূমির স্মৃতিগুলিও শতকরা বিশ ভাগ মনে আছে? নেই। এখানকার ম্মৃতিই তাহলে আর মনে থাকবে কেন? এমনিতেই আমার দুর্নাম আছে, আমি যত তাড়াতাড়ি কাউকে আপন করে নেই, পরে তার চেয়েও বেশী বেগে তাকে পর করে দেই! কতক্ষণ হাঁটলাম? আমি ঘড়ি বা মোবাইল কোনটা নিয়েই বাইরে বেরুই না। কোনকালেই এ অভ্যাসটি আমার হল না।
জার্মানির শহরে, বাজারে, রাস্তার মোড়ে সর্বত্র ঘড়ি আছে। নিজের ঘড়ি না থাকলেও সময় জানতে কোন অসুবিধা হয় না। বাসায় আমার নানা ধরনের ৭-৮টি ঘড়ি। এক ঘরের বাড়িতে প্রায় প্রতিটি কোনে, টেবিলে, দেয়ালে, রান্নাঘরে, বাথরুমে, বিছানার মাথার দিকে, পায়ের দিকে। ঘরে বসে কম্পুটারে কাজ করার সময়ও পর্দায় সব সময় ঘড়ি থাকে। কিন্ত বাইরে এসে আমি ঘড়িকে কোন গুরুত্ব দেই না কেন? রাস্তাটি স্কেলের মত সোজা। সামনে পেছনে তাকালে ১-২ কিলোমিটার নজরে আসে। কিন্ত গাছপালা, পাখপাখালি ছাড়া কোন প্রানী চোখে পড়ে না। একটা কাঠবিড়ালী ছাড়া আর তো জ্যান্ত কিছু দেখলাম না।
বনের এ রাস্তাটি কোন জনপ্রিয় আন্ত-শহর বেড়ানোর রুটে পড়ে না। শহরের পাশে জঙ্গলের মধ্যে এটা নেহায়েতই একটা ছোটখাট পায়ে চলার পথ। শুরু এ শহর থেকেই। শেষ দশ কিলোমিটার পরে বিটবুর্গ সড়কে। বিকেলের দিকে রোদের তেজ কমলে বেড়াতে আসেন কেউ কেউ। শনি-রবিবারেও, সপরিবারে বাচ্চাকাচ্চা নিয়ে আসেন। আজ রবিবার কিন্ত সাঙ্ঘাতিক গরম। এ সময়ে অনেকেই বিছানা থেকেই উঠেনি। হঠাৎ মনে হল, গাছেরা আমার দিকে বিষ্ময়ে তাকিয়ে আছে। অসময়ে, এত সকালে, গরমের মধ্যে এ কে? একা হেঁটে যাচ্ছে? পিপাসা লাগল কি? না। ক্লান্ত বোধ করছি কি? সকালে দু‘পিস টোষ্ট খেয়েছি। মনে হল কখন হজম হয়ে গেছে। ব্যাগে বিস্কুট-আপেল আছে। কিন্ত দাঁড়িয়ে ব্যাগ কাঁধে থেকে নামিয়ে ওসব বের করতে রাজ্যের আলসেমী এসে গেল।
ঠিক মাঝামাঝি, ছয় কিলোমিটার ফলক যেখানে, সেখানে এই এলাকার বিখ্যাত লিন্ডে গাছটি আজ চারশ বছর ধরে ডালপালা মেলে দাঁড়িয়ে আছে। বনবিভাগ থেকে পর্যটকদের জন্য তার চারদিকে কাঠের বেঞ্চ বসানো আছে। পাশেই একটা পানির নল আছে। বনের মধ্য থেকে একটা ঝরনার পানিকে ঐ নল দিয়ে লিন্ডের পাশে একটু জায়গা পাথর দিয়ে ঘিরে নিয়ে আসা হয়েছে। দিনরাত চব্বিশ ঘন্টাই পানি পড়ে। দু‘টি পাথরের মাঝ দিয়ে পানি নিঃসরণ হয়ে বনে ছড়িয়ে পড়ছে। আশেপাশের ঝোপঝাড়, গাছগুলির পিপাসায় কাতর হবার কোন সম্ভাবনাই নেই। সবচেয়ে উপকৃত লিন্ডে। সে সবচাইতে সিনিয়র এবং সাইজেও বড়। সৌরজগতে সুর্যের মত! পানির পরিমান তারই লাগে সবচাইতে বেশি। নিশ্চয়ই যে পানিকে ঝর্ণা থেকে নল দিয়ে বাইরে এনেছিল, সে সযতনে ধারাটির অবস্থান লিন্ডের পাশেই করে দিয়েছে। মনে মনে বৃক্ষপ্রেমী এই মহান ব্যক্তিকে আমি আন্তরিক ধন্যবাদ জানালাম। শুধু লিন্ডেই নয়, এই পথ চলতে শ্রান্ত হয়ে যারা লিন্ডের ছায়ায় বেঞ্চে বসবে, তারাও পিপাসা নিবারন করতে পারছে। আমার ধারনা, কিছুক্ষনের মধ্যেই ওখানে পৌছব। তারপরই বেঞ্চে বসে, প্রাণভরে পিপাসা, ক্ষুধা দু‘টিই মেটাবো। চিন্তাটা করার পরই ক্লান্তি, দেহের অবসাদ সব কমে গেল। অজান্তেই গুণ গুণ করে কি যেন একটা গানও গাইলাম, মনে হয়!
স্বপ্নের জোড়া পাহাড়
বেঞ্চে কখন শুয়েছি, কখন ঘুমিয়ে পড়েছিলাম তা টের পাইনি। পরিশ্রান্ত হলে দেহের বেশ কিছু অঙ্গ কাজ করতে চায় না। সাথে সাথে কিছু ইন্দ্রিয়ও বিদ্রোহ করে, তারাও বিশ্রাম চায়। একমাত্র পরিণাম, শুয়ে পড়া এবং তারপর নিদ্রার হাতে দেহমনকে সঁপে দেয়া। বাহ্যিক পৃথিবীর সাথে সমস্ত সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন করে সবকিছু থেকে নিজেকে হারিয়ে ফেলা! নিদ্রা আর মৃত্যুর মধ্যে একটাই পার্থক্য- নিদ্রার শক্তি সীমাবদ্ধ। যতই ঘুম হোক না কেন, এক সময় ভাঙ্গবেই। নিজের থেকে বা অন্য কারো ডাকাডাকি বা ঠেলাঠেলিতে নিদ্রার শক্তি কমে যায়। অবশ্য সে সহজে ছেড়ে দেয় না। নিদ্রিতকে যতটা পারে ঘুমের রাজ্যে রেখে দিতে চায়। কিন্ত চেতনা নাছোড়বান্দা। তারপর যদি কেউ ধাক্কাধাক্কি করে বা শব্দ করে, না উঠে এই অস্বস্তিকর পরিস্থিতির অবসান হয় না। অবশ্য যারা ঘুমের সমস্যায় ভোগেন, তাদের কথা আলাদা। তারা তো কখনই পুরো ঘুমের স্বাদ পান না। পাতলা ঘুম, শব্দের প্রতি অতিরিক্ত সংবেদনশীলতা এসবই গভীর নিদ্রার বিরুদ্ধে। ট্যাপের ফোটা ফোটা পানির শব্দে ঘুম ভেঙ্গ যায় বা ঘুম আসে না, এসব অভিজ্ঞতা আমার ব্যক্তিগতভাবে বহুবার হয়েছে। আমার এসব কোনই সমস্যা নেই। চিরদিন, বড় ছোট মাঝারি স্থানে, এমনকি চেয়ারে বসেও ঘুমিয়ে পড়ি। বয়সের ভারে এখন ঘরে সোফায় বসেই সারা দিনরাতের অর্ধেক ঘুম হয়ে যায়।
নিদ্রার একটি ঘনিষ্ঠ সঙ্গী হল স্বপ্ন। ঘুমের সময় শরীর খুলে দেয় আত্মার গোপন পৃথিবীর একটি জানালা- একটি পথ উন্মুক্ত হয়, অবচেতন মনের সূ² গুপ্তধনের দিকে। এটি এখানে, সময়হীন অভিজ্ঞতার গুপ্ত গভীরে, অতীতের ধূমায়িত অসন্তোষ ধিকিধিকি করে জ্বলে, কল্পনার ভাবজাগতিক ইঙ্গিত, সঙ্কট নিরসনের আকাক্সক্ষা, সব এসে একসাথে ভিড় করে।
বিশেষজ্ঞরা বলেন, রাতের স্বপ্নে বেশির ভাগ ঘটে যাওয়া বিষয়গুলির আবির্ভাব ঘটে। অর্থাৎ দূর বা নিকট অতীতের স্পর্শকাতর অভিজ্ঞতার পুনরায় আবির্ভাব ঘটে। দিনের স্বপ্নে দূর বা নিকট ভবিষ্যতের ইশারা থাকে। অস্পষ্ট কিন্ত দুর্বোধ্য নয়। ঐ দিনে আমিও এরকমই কিছু ইঙ্গিত পেয়েছিলাম। পরের দিনগুলোতে অবাক, অবিশ্বাস্য, বিস্ময়কর সব ঘটনা যখন ঘটল- আমার আজকের দিনের বনের মধ্যে শুয়ে টুকরো টুকরোভাবে স্বপ্নে যা দেখেছিলাম, তাদের বেশ কিছ পুনরাবৃত্তি হয়েছিল। যথাসময়ে বলব।
গত আটচল্লিশ বছরের দীর্ঘ প্রবাসজীবনে (১৯৭৭ সাল থেকে) আমি একা এবং সঙ্গীনিসহ ইউরোপের অধিকাংশ বড় শহরেই গিয়েছি। উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকার নিউইয়র্ক, মেক্সিকো, আর্জেন্টিনা, ব্রাজিল ও কিউবাতে যাবার সৌভাগ্য হয়েছে। অস্ট্রেলিয়াতেও দু’বার গিয়েছি। আমার এই বিশ্বভ্রমণে এখনও আফ্রিকা মহাদেশ বাদ রয়েছে এবং সবচাইতে উল্লেখযোগ্য দুর্ভাগ্য হল প্রিয় জন্মভুমি বাংলাদেশ ছাড়া এশিয়ার কোন দেশেই এখনও যাওয়া হয়নি। এমনকি ’৭১-এর রক্তাক্ত মুক্তিযুদ্ধের সময়ও ভারতে যাইনি। স্বাধীনতা যুদ্ধের শুরুতে সেসময় একবার পাক মিলিটারির হাতে পাবনাতে দু’রাত বন্দীও ছিলাম। তবুও দেশত্যাগের ঝুঁকি নেবার সাহস হয়নি। আসলে আমি একেবারেই একটি ঘরকুনো লোক। আমার নানী বলতেন, আমার পাছায় নাকি আঠা লাগানো, যেখানে বসি সেখান থেকে আর উঠতে মন চায় না! ঢাকা শহরে চাকরি উপলক্ষে বাংলাদেশে শেষ সময়টি কাটানোর সময় এক পাথর ছোঁড়ার দূরত্বে বড় ভাইয়ের বাসায় নিয়মিত যেতাম। প্রধান কারণ ছিল, প্রায়ই চাকরি থাকত না সেসময়। ভাবীর কাছে সংসার খরচের জন্য হাত পাততে হতো প্রায়ই। এছাড়া ভাবী আমাকে খুব আদর করতেন, তার হাতের রান্না খাবারেরও লোভ ছিল। আমি মনে করি এই মহিলাটি আমাকে আমার নিজের মায়ের চাইতে বেশি স্নেহ করতেন। আমার জীবনে আমি যেসব মহিলার সান্নিধ্যে এসেছি- বাঙালি মহিলার সাথে বিয়ে হয়েছে দু’বার, জার্মান সঙ্গিনীর সাথে দীর্ঘ আঠারো বছরের লিভিং টুগেদার হয়েছে- এরা ব্যতীত আমার নিকটাত্মীয়দের মধ্যে আমার নানী ছিলেন আমার সবচাইতে প্রিয়। এই নিরক্ষর বৃদ্ধা আমার জীবনের প্রথম শিক্ষক। তাঁর কাছে যে কত কিছু শিখেছি, জেনেছি, তার লেখাজোখা নেই। নিঃস্বার্থ ভালোবাসা, নিঃশর্ত স্নেহ, অন্ধ আবেগ আর অফুরান আদরের নিরংকুশ প্রমাণ। নানার বাড়ি ছিল জামালপুর শহরের পুরোনো ব্রহ্মপুত্রের (এখন নদীটি শুকিয়ে গিয়ে শহরের অংশ হয়ে গিয়েছে) ওপারে তিন মাইল দূরে। আমার মনে আছে শুধু হাফ প্যান্ট পড়ে খালি গায়ে আর খালি পায়ে নদী পার হয়ে হেঁটে হেঁটে, বয়স কতই হবে তখন ৭/৮ নানার বাড়ি বহুবার চলে গিয়েছি। স্কুলে যাবার নাম করে, উল্টো পথে চুপে চুপে গিয়েছি। পরিণামে বাবা-মার চেলা কাঠের পিটুনি এখনও পিঠে ব্যথা করে! বিবাহিতা স্ত্রীদের কাছে যখন কারণে অকারণে অভিযোগ, অনুযোগ আর অবহেলা পেয়েছি তখন শুধু নানী আর ভাবীর কথা মনে হতো। এরা তো কখনই আমাকে, শত অপরাধ সত্ত্বেও, অনাদর করেননি!
ঢাকা শহরে আমার দু বোনই যার যার সংসার নিয়ে বাস করতেন। অনেক বন্ধু ছিল। কিন্ত আমি এদের কারো বাসায় পারতপক্ষে যেতাম না। নিজের বাসায়, নিজের ঘরে বইপুস্তক নিয়ে বসে আর পত্রিকা পড়ে, রেডিওতে গান শুনে, এসবে যে আনন্দ পেতাম তার বিপরীতে আত্মীয় বন্ধুদের নিমন্ত্রণ আমার কাছে কোনো গুরুত্বই পেত না। সেই আমি ’৭৭ সালের এক ফেব্রুয়ারি মাসে, বিশেষ পরিস্থিতিতে অনিবার্য কারণে প্রায় চোরের মতই দেশত্যাগ করেছি! তখন কথা ছিল, কয়েক মাস পরেই আমাকে দেশে ফিরিয়ে নিয়ে আনা হবে! সেই কয়েক মাস আজও পূর্ণ হয়নি! ৪৫ বছর প্রায় হয়ে গেল! একটানা তিরিশ বছর জার্মানিতে থাকার পর ২০০৮ সালে দেশে গেলাম। প্রথম বইটি প্রকাশিত হয়েছেল সে বছর বইমেলায়। উপলক্ষ্য সেটাই ছিল। ততদিনে আমি জার্মান নাগরিক! বিদেশীনি আর সঙ্গে নেই। এর মধ্যে সুইজারল্যান্ডে চার বছর কাটিয়েছি। একে একে মা (বাবা আগেই ৭২ সালে মারা গিয়েছিলেন), ভাবী, ভগ্নিপতি, বড়বোন, বড়ভাই, সব চাচা, খালা, অনেক ঘনিষ্ঠ বন্ধুবান্ধব দেহত্যাগ করলেন। কারো সাথেই মৃত্যুশয্যায় আমার দেখা হয়নি। প্রবাসজীবন বড়ই নিষ্ঠুর! আমার প্রজন্মে এখন শুধু আমিই একা বেঁচে আছি। কালের সাক্ষী বটবৃক্ষ! দেশে আমার একজন নাতীও মারা গেছে। এবং আমার দৃঢ় বিশ^াস, আরো অনেক স্বজন এখন আর এ দুনিয়াতে নেই, আমি জানি না!
গত বছর আমার ছোটবোন ফ্লোরিডায় দীর্ঘদিন রোগে ভূগে মারা গেলেন। আমরা দু’ভাই, দু’বোনের মাঝে ছিলাম। ছোট বোন মিনা ও আমি পিঠাপিঠি। তাকে দিয়েই আমার এ কাহিনীর সূত্রপাত। ৬৫-৬৬ বছর আগে, জামালপুরে।
জার্মানিতে যখন সঙ্গীনির সাথে একত্রে থাকতাম, সেসময় এক শীতের সন্ধ্যায় উষ্ণ ঘরে সোফায় বসে আমরা সান্ধ্যাহারের পর জাবর কাটছিলাম। কথায় কথায় সঙ্গীনি প্রশ্ন করল, যে সব শহরে আমরা বেড়াতে গিয়েছি, তার মধ্যে কোনটা আমার সবচাইতে ভালো লেগেছে। আমি বিন্দুমাত্র চিন্তা না করে বললাম, একটাও নয়! বান্ধবী তো সাত বাঁও পানির নিচে! সেকি? ইউরোপেই তো আমরা অন্তত কুড়ি-পঁচিশটি শহরে বেড়াতে গিয়েছি। প্যারিস, রোম, লন্ডন, মস্কো, অসলো, কোপেনহেগেন, ব্রাসেলস, জেনেভা, আরো কত! এর মধ্যে একটাও তোমার ভালো লাগেনি? কেনো? আমি বললাম- কারণ একটাও আমার প্রিয় শহর জামালপুরের মত নয়! বিষ্ময়ে ও অবিশ্বাসে ওর চোখদু’টি যেভাবে বিস্ফোরিত হয়ে গেল, আমার আশংকা হয়েছিল, ফেটে না পড়ে! আমি অনেক সময়েই জামালপুরের কথা ওকে বলেছি। আমার বহু লেখাতেও এর স্মৃতিচারণ আছে। এই শহরে আমার জন্ম না হলেও, এক বছর বয়েস থেকে মেট্রিক পাশ পর্যন্ত (১৯৪৬-১৯৬১) আমি এ শহরেই বড় হয়েছি। তখন স্টেশান থেকে হাসপাতাল পর্যন্ত এক রাস্তার এই মফস্বল শহরটিতে এসডিও বাহাদুর ও আরো কয়েকটি সরকারী অফিসারদের বাসা ছাড়া আর কোন পাকা বাড়ি ছিল না। আমাদের বাসাও ছিল বাঁশের বেড়া আর টিনের চালের। আমাদের স্কুল, জামালপুর সরকারী হাই স্কুলটিতে হেড মাস্টার, টিচারদের ঘর, লাইব্রেরি ও ক্লাস টেন ছিল একটি পাকা দালানে। সায়েন্স ল্যাবরেটরিটি ছিল পাকা। ক্লাস নাইন পর্যন্ত আমরা টিনের চাল ও বাঁশের বেড়ার ঘরে ক্লাস করেছি। টানা পাখা চলত ক্লাস চলার সময়। টিউবওয়েল ছিল না। বড় একটা বাঁধানো কুয়া ছিল, উপরে ছিল কাঠের ঢাকনি। পাশেই ছিল দু’টি পানি খাবার টিনের ঘর। একটি মুসলমানের আরেকটি হিন্দুর (বিশ্বাস হয়?)। দু’ঘরেই কুয়াটি থেকে মাটির কলসে পানি ভরে রাখা হত এবং ৩/৪টি এনামেলের গ্লাস থাকত। আমরা ক্লাস চলার সময়ে স্যারকে বলে (অল্প সময়ের ছুটি) পানি খেতে আসতাম এই ঘরে। শহরের রাস্তায় দু’টি রিকশা দু’দিক থেকে যাতায়াতের সময় প্রায়ই রিকশাচালকরা নেমে ঠেলে ঠেলে রিকশা নিয়ে যেত। এত সরু রাস্তা। এসডিও সাহেব আর এসডিপিও সাহেবের দু’টি জিপ ছিল। এগুলি যখন চলত, আমরা বিষ্ময়ে দাঁড়িয়ে থেকে দেখতাম! মহিলারা রিকশায় চলতেন পর্দা টানিয়ে। বাড়ির চাকর বা ছোট্ট ছেলে/মেয়েরা রিকশার পা-দানিতে (শৈশবে আমরাও) বসত। আরেকটি বিখ্যাত গো-শকট ছিল মিউনিসিপ্যালিটির গরুর গাড়ি! চালক একজন মেথর। দিনের বেলায় সে গান গাইতে গাইতে প্রকাশ্যে গাড়িটি চালিয়ে বাড়ি বাড়ি থেকে মল সংগ্রহ করত। গাড়িটিকে বলা হতো গুয়ের গাড়ি! আজ যখন বাংলাদেশে শতকরা ৯৯টি বাড়িতে স্যানিটারি ব্যবস্থা তখন সেকালের এই সত্যটি হজম করা বেশ কঠিন।
বাবা ছিলেন রাশভারী, মা প্রায় নিরক্ষর, রান্নাঘর আর ঘরকন্না নিয়ে রাতদিন ব্যস্ত থাকতেন। বাসায় সব সময় ২/৩ জন চাচা, খালা থাকতেন। খাবার-দাবার ছিল খুবই সাধারণ। এখন বিনোদন বলতে যা বোঝায়, বাসায় তার ছিটেফোঁটাও ছিল না। তাই আমি আর মিনা এদিকে সেদিকে দৌঁড়াতাম। প্রতিবেশী বা আত্মীয়দের বাড়ি বেড়াতে যেতাম। বাসার আবহাওয়ায় বলতে গেলে দম বন্ধ হয়ে আসত। প্রতিদিনের রুটিন একঘেয়ে, থোর বড়ি খাড়া, খাড়া বড়ি থোর! সকালে বিস্বাদ রুটির নাস্তা, সাথে রাতের বাসি তরকারি। প্রধান খাদ্য ভাজি, ডাল আর সব্জী! শুক্রবারে বাবার মর্জি হলে কোনদিন গরুর মাংস বা মাছ। এখন বুঝি, বাবা যদিও স্থানীয় কলেজের প্রিন্সিপ্যাল ছিলেন, বাসায় খানেওয়ালা অনেক। বাবা এবং মায়ের পক্ষের আত্মীয়রা প্রায়ই শহরে নানা কাজে এসে আমাদের ওখানেই খাওয়া-দাওয়া করতেন। বাবার একার রোজগারে কুলাত না! এর মধ্যে দাদা প্রায়ই এসে টাকাপয়সা নিতেন। গুমোট হাওয়ার মধ্যে শীতল বাতাস ছিল নানী যখন এটাসেটা, পিঠা, চাল, দুধ, চাল, তরী-তরকারি পাঠাতেন। বড়মামা সাইকেলে করে নানা টোপলা নিয়ে আসলেই আমরা খুশী হয়ে যেতাম। আজ ভালো কিছু একটা খাওয়ার সম্ভাবনা আছে! নানা প্রাক্তন সরকারী স্কুল শিক্ষক। জন্ম থেকেই দেখতাম তিনি মাসে একবার শহরে এসে ট্রেজারি থেকে পেনশন নিতেন। সম্পন্ন গৃহস্ত, বেশ জমি ছিল তার। নিজেই খেতে হাল চালাতেন। দুই মামার একজন শিক্ষক আরেকজন কৃষক। তিন ভাই-এর এক বোন, আমার মা। ছোট ভাইটি ময়মনসিংহ জেল্ াশহরে ওভারশিয়্যার (ছোট পদের ইঞ্জিনিয়ার) ছিলেন। বোনকে সবাই তারা খুব আদর করতেন। তার ভাগ আমরা পেতাম। এরা সব আমার বড় নানীর সন্তান, যিনি বহু আগেই মারা গিয়েছিলেন। বর্তমান নানীর ছিল মোট আটটি মেয়ে। তার ছেলে ছিল না। এক ˜ঙ্গল খালা! এদের মধ্যেই আমরা বড় হয়েছি। সৎ নানী, মার সৎ বোন এসব আমরা কোনদিন শুনিনি। আমি বহুদিন বুঝিইনি যে এরা সব সৎ! আমার নানীকে তো সৎ বলার প্রশ্নই উঠে না। আমার সবচাইতে আপন আত্মীয়। আমার আজও সব স্পষ্ট মনে আছে!
আমার শৈশব আমার ছোটবোনকে ঘিরে গড়ে উঠেছে। খেলার সাথী, নিত্য ঝগড়ার প্রতিপক্ষ। মিনা ছোট থেকেই খুব মিথ্যা কথা বলত। বেশ কুটনি টাইপ ছিল! নিজের সামান্য স্বার্থেই অম্লানবদনে মিথ্যা কথা বলত। অবশ্য আমাদের পরিবারে কমবেশী সবাই মিথ্যা কথা বলত। আমিও বলতাম। হয়ত এখনও বলি! একমাত্র ব্যতিক্রম ছিলেন আমার বড় বোন। বড়ভাইও অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে অসত্য বলতেন। আমার এক খালাকে তো সে সময়েই মনে হতো মিথ্যা বলার বিশ্বচ্যাম্পিয়ন! চুপে চুপে বলি, আমার বাবাও...। এসব বিবেচনা করলে আমার পরিবারকে একটা অভিশপ্ত পরিবার বলে মনে হয়। যাক, সবাই মারা গেছেন। এসব বলার আর কি দরকার? তবে মিনা আমাকে খুব ভালোও বাসত। টের পেতাম, যখন কেউ আমাকে মন্দ বলত বা সমালোচনা করত। সেটা সে কোনমতেই সহ্য করত না। মাঝে মাঝে সে বলত এবং এ কথাটি সে পরেও বলেছে, আমার ভাই আমি যা খুশী বলব, তাই বলে অন্য কেউ কেন আমার ভাইকে খারাপ বলবে! আমার দুই ভাইয়ের মত প্রতিভা আর কার আছে? লাখে একজন ওরা ইত্যাদি! আজ ওর কথা মনে হলে খুব কষ্ট হয়। আমাদের ভুল বোঝাবুঝিই বেশি হয়েছে। আমি ’৭৭ সালে দেশ ছেড়ে চলে এলাম। ও মনে হয় ২০০১ কি ২০০২ সালে আমেরিকা চলে গিয়েছিল। তারপর মনে হয় আমাদের দু’বার কি তিনবার দেখা হয়েছে! ২০০৪ সালে আমেরিকায় ওর সাথে সম্ভবত আমার শেষ সাক্ষাত হয়েছে। ওর দু’টি মেয়ে এখন কোথায় আছে তাও ঠিক জানি না! সময়ের ধারায় সব মায়া মমতা, স্নেহ ভালোবাসা ভেসে যায়!
যা বলছিলাম। মিনা আর আমি দু’জনে সারা শহর চষে বেড়াতাম। তখন বৃষ্টি হতো একটানা ৩-৪ দিন। শহর ভেসে যেত! আমরা দুই ভাই-বোনে বৃষ্টির সুযোগ নিয়ে প্রতিবেশীদের বাগান থেকে ফুল গাছ চুরি করে উপড়ে তুলে নিয়ে এসে আমাদের বাগানে রোপন করতাম। এভাবে আমাদের বাগানে নানারকমের ফুলের গাছের সমাহার দেখার মত ছিল! একবার আমরা একটি ছোট্ট কদম গাছের চারা চুরি করে এনে আমাদের বাসার সীমানায় লাগিয়েছিলাম। আমি দেশ ছেড়ে আসার সময়ই বেশ প্রকান্ড হয়ে গিয়েছিল সে গাছটি। মনে হয় ১৯৮৫ সালের দিকে গাছটি আমার মা দেশলাই কারখানার লোকদের কাছে বেঁচে দিয়ে বিরাট পরিমাণের একটি অর্থ রোজগার করেছিলেন। বড়বোন ফোনে আমাকে জানিয়েছিলেন। গাছটি নাকি এতই বড় হয়েছিল যে বহু দূর থেকে দেখা যেত! বর্ষার সময় সারা গাছে কদম ফুলে সাদা হয়ে যেত। বড় বোন অনুনয় করে মাকে বলেছিলেন, গাছটি হারুন আর মিনার হাতে লাগানো, বিক্রি করে দেয়া ঠিক হবে না। ও তো একদিন ফিরে আসবেই। এসে যদি গাছটি দেখতে চায়? একটা স্মৃতির ব্যাপার আছে। মিনা নাকি বিক্রির টাকার একটা অংশ পাওয়ার প্রতিশ্রুতি পেয়ে চুপ করে ছিল এবং আমার মা ভাবলেশহীনভাবে মন্তব্য করেছিলেন, ওকি আর দেশে কোনদিন ফিরবে? আর ফিরলেই কি এই গাছের কথা ওর মনে থাকবে? আমার মার কিছু কিছু মন্তব্য, আজব ব্যাপার আজও আমার কাছে অবোধ্য। তার হৃদয়হীনতা, মমত্ববোধের অনুপন্থিতি আজও আমাকে পীড়া দেয়। যাক আগেই বলেছি, আমাদের পরিবার একটি অভিশপ্ত পরিবার! এই সব দুঃস্মৃতি স্মরণ করার জন্য আজ আমিই শুধু একা বেঁচে আছি! (চলবে)
নয়ে-ইজেনবুর্গ, জার্মানি ২০ ডিসেম্বর, ২০২১
গতসংখ্যার লিংক: http://www.amadermanchitra.com/details.php?newsID=220110093643823