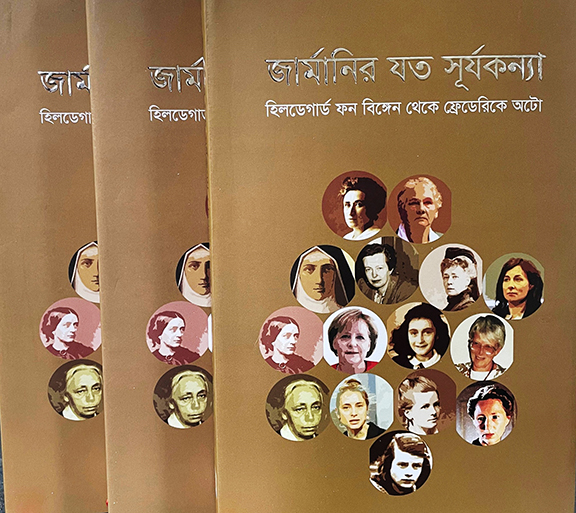আবদুল্লাহ আল-হারুন:
পটভূমিকা
বিশ্বাস এবং জ্ঞানের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করা খুব একটা সহজ ব্যপার নয়; যেমনটা বোধ এবং উপলব্ধির মধ্যে হয়ে থাকে। পদার্থবিদ্যার নতুন কোন থিয়োরি প্রথমে অনুমানের মধ্যে জন্ম নেয় এবং পরে ক্রমে প্রমাণের মাধ্যমে হয় নিশ্চয়তা লাভ করে, নতুবা বাতিল হয়ে যায়। কিন্তু বিশ্বাসের বেলায় এটা প্রযোজ্য নয়। ‘আমি বিশ্বাস করি’, এর অর্থ একটাই- যার কোন বিকল্প নেই। উদাহরণ ইসলাম ধর্মের প্রধান ভিত্তি ও অস্তিত্ব যার উপরে নির্ভরশীল, সেই কোরান শরীফের প্রথম সূরার প্রথম অধ্যায়ে ‘মোমিনের’ সংজ্ঞা নির্ধারণে যে পাঁচটি শর্তের উল্লেখ আছে, তার মধ্যে প্রথমটিই হল, ‘অদৃশ্যের উপরে বিশ্বাস করা’। তারপর অন্য চারটি। এজন্যই বিশ্বাস বজায় রাখা যেমন সহজ তেমনি একে বদলানো খুবই কঠিন। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় যারা একে অপরকে হত্যা পর্যন্ত করতে উদ্যত হয়, সেখানে প্রধান শক্তি হিসেবে কাজ করে ‘অন্ধ ও আপোষহীন বিশ্বাস।’ এজন্যই অনেক বিশেষজ্ঞ ধর্মকে বিজ্ঞানের সঙ্গে এক সাথে আলোচনা করতে নারাজ।
বোধ এবং উপলব্ধির মধ্যেও পার্থক্য খুবই সূক্ষ্ম এবং যুক্তিতর্কের ঊর্ধে।
দৃষ্টি এবং দৃষ্টিবিভ্রমের মধ্যেও প্রভেদ করা মাঝে মাঝে অত্যন্ত কঠিন। বিশেষ করে শারীরিক ও মানসিক উভয় ক্ষমতাই যদি কখনও এলোমেলো হয়ে যায়। আমাদের পার্থিব জীবনকে অনেক দার্শনিক অলীক এবং বিশ্বব্রহ্মান্ডের কোন বৃহৎ শক্তির হাতের খেলা (কম্পিউটার গেম) বলে মনে করেন। ‘যা দেখছি তা সত্য নয়, যা দেখছি না, তাই সত্য’- সনাতন হিন্দু ধর্মের ‘মায়া-দর্শনে’ও তারই প্রতিফলন। ইসলাম ধর্মের সূফি মতবাদেও তার স্বীকৃতি পাওয়া যায়। তথাকথিত ‘মেট্রিক্স’ বাস্তবতাতেও এর প্রতিফলন ঘটেছে। বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক কল্পকাহিনীতে বিভিন্ন ডাইমেনশনের কথা বলা হয়। অ্যালিয়েন, রোবোট, ভিন্ন গ্রহের জীবন এখন পর্যন্ত সবই অলৌকিক এবং আমাদের দৈনন্দিন জীবনের ধরাছোঁয়ার বাইরে। গত শতাব্দির শুরুতে আইনস্টাইনের ‘বিশেষ ও সাধারণ আপেক্ষিক তত্ত¡’ আবিস্কারের পর ‘টাইম-ট্র্যাভেল’ এর মত কিছু ‘অবোধ্য’ ও ‘বিতর্কিত’ বিষয় গবেষণা ও পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে ‘থিয়োরিটিক্যালি’ প্রমাণিত হয়েছে, যদিও এর দ্রুত বাস্তবায়ন হবার কোন সম্ভাবনা নেই। কিন্ত ভবিষ্যতে কোন এক সময়ে যে মানুষ গ্রহ থেকে গ্রহান্তরে এবং আন্ত-গ্যালাক্সি ভ্রমণ করবে, সৌর জগতের বাইরে বসতি স্থাপন করবে তা একরকম নিশ্চিতই বলা যায়। আজকাল অধিকাংশ পদার্থবিদ ‘টাইম-ট্র্যাভেল’কে তাই বাস্তবসম্মত ও সম্ভব বলে মনে করেন।
বর্তমানে মানুষ তার জীবনকে প্রায় সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে নিয়ে এসেছে। দৈনন্দিন জীবনে বিজ্ঞানের অবিশ্বাস্য উত্তরণ- কম্পিউটার, মুঠোফোন, নানাধরনের সহায়ক-টেকনোলজি জীবনের মান, আয়ু, স্বাস্থ্য, চিকিৎসা, মহাশূন্যের গবেষণা ইত্যাদির মাধ্যমে গত একশ বছরে মানব-সভ্যতাকে এক অভাবনীয় উচ্চে তুলে নিয়ে এসেছে। যুদ্ধ, ধ্বংস, শোষণ, অবিচার, ক্ষুধা, দারিদ্রকে পূর্ণভাবে দূর করা যায়নি কিন্ত মানুষের সচেতনতা, আত্মসম্মানবোধ, শিক্ষার বিস্তার, যোগাযোগ ব্যবস্থা, বিশেষ করে নারী স্বাধীনতার অগ্রগতি প্রায় সর্বত্র প্রতীয়মান। খাদ্য, বাসস্থান, অধিকার, জীবন-যাপনে স্বাচ্ছন্দ্য, প্রতিবেশের প্রতি মনোযোগ ইত্যাদি বর্তমান যুগের উল্লেখযোগ্য প্রাপ্তি।
কিন্ত এত কিছুর পরেও মানুষ তার জীবনের ‘প্রারম্ভ’ এবং ‘শেষ’কে নিয়ন্ত্রণে আনতে পারেনি এবং (মনে হয়) কোনদিন পারবেও না। আমি জন্ম ও মৃত্যুর কথা বলছি। কেউ জানে না ‘কেন কোথায়, কখন’ তার মাতৃজঠরে আবির্ভাব ঘটেছিল। বায়োলোজিক্যাল ব্যাখ্যা অবশ্যই আছে কিন্ত, সন্তানের সংখ্যা হয়ত নির্ধারণ করা সম্ভব (জন্ম নিয়ন্ত্রন) কিন্ত জন্মমুহূর্তের নির্দিষ্ট সময়টির আন্দাজ করা বা যে সন্তানটি জন্ম নিল, তার কাছে সে সময়টি সব সময়েই অজানা থেকে যায়। জন্ম মুহূর্ত, রাশি, নক্ষত্র সবই সে বাবা মা বা অন্যদের কাছে শুনে থাকে। এবং প্রগতির বর্তমান চরম উন্নয়নের সময়েও পৃথিবীর ক’জন তার সঠিক জন্মদিনটি জানে? অন্তত আমি যে জানি না তার প্রমাণ, আমার মরহুম বাবা-মা/বড় ভাই-বোন বা অন্য জৈষ্ঠরা আমার জন্মদিনকে একেকজন ভিন্ন ভিন্ন তারিখ বলে উল্লেখ করতেন। আমার বহু অনুনয় বিনয়ের পরেও তারা একমত হন নি। শেষপর্যন্ত মেট্রিক পরীক্ষায় ফর্ম ফিলাপের মুহূর্তে (আমাদের সময়ে তখনি প্রথম জন্মদিন লেখার প্রয়োজন হতো) বাবার বলা তারিখটি স্থায়ীভাবে আমার জন্মদিন হয়ে যায় এবং এখনও তাই আছে। যদিও জীবদ্দশায় আমার মা ও বড়বোন দৃঢ়ভাবে তার প্রতিবাদ করতেন। সে তর্কের বহুদিন আগেই অবসান হয়ে গেছে। তারা সবাই এখন মৃত। ইউরোপ/আমেরিকার কথা স্বতন্ত্র। এখানে শতকরা ৯৯.৯টি সন্তানই হাসপাতালে জন্ম নেয়। জন্মলগ্ন থেকেই বিভিন্ন ধরনের রেজিস্ট্রেশান শুরু হয়ে যায়! সেজন্যই এদের জন্ম এবং মৃত্যুর দিনক্ষণের হিসেবের গোলমাল হয় না! আমাদের দেশেও এখন ইলেক্ট্রনিক নিবন্ধন শুরু হয়েছে। কিন্ত সেগুলি কতটা বাস্তবিক তা প্রশ্নসাপেক্ষ! কিন্ত আমি সরকারি নিবন্ধনের কথা বলছি না, যা তৃতীয় পক্ষ করে থাকে। আমার কথা হলো, কখন আপনি মারা যাবেন, তা আপনি আপনার জীবনে কখনই নিশ্চিত হতে পারেন না। আপনার জন্মদিনের খবর যেমন আপনি আরেকজনের কাছে শুনে থাকেন, আপনার মৃত্যুর দিনটিও আপনার অজান্তেই আসবে, জানবে অন্যরা আপনি নন! মরণের পরে অন্য ভূবনে গিয়ে আপনি তা অবগত হবেন কিনা, তা কেউ জানে না। কারণ সেখান থেকে কেউ ফিরে আসে না, কেউ কোনদিন আসবেও না। এটাই মানবজীবনের পরম, চরম এবং সবচাইতে বড় সত্য। এটা যত বেশি করে বিশ্বাস করবেন, ততই আপনার ‘মৃত্যুভয়’ কমে আসবে! যারা পুনর্জন্মে বিশ্বাস করেন, তাদের কাছে ক্ষমা চেয়ে বলছি, আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত মৃত্যুগবেষকরা মরণের পরে আরেকটি জীবনে বিশ্বাস করেন, তার প্রমাণও রয়েছে অনেক। তবে সে জীবন অন্য আরেকটি ভূবনে, এখানে এই পৃথিবীতে নয়। দুঃখের বিষয় হল, সেখানে গিয়ে কেউ আর এখানে ফিরে আসে না, স্বপ্নের কথা স্বতন্ত্র। তাই সে ভূবন চিরদিন জীবিতদের কাছে অজানা হয়েই থাকবে।
চিকিৎসকরা এখন মানব শরীরের হৃদয়, চক্ষু, কর্ণ সব কিছু বদলে দিতে পারেন। প্লাস্টিক সার্জারি, ওপেন হার্ট অপারেশন এখন ডালভাত! আমারও হয়েছে ২০১২ সালে! ক্রোধান্বিত হয়ে ভৃগু ঋষি দেবাদিদেব মহাদেব শিবের বুকে লাথি মেরেছিলেন, ‘বিদ্রোহি’ কবিতায় কাজী নজরুল ইসলাম তার উল্লেখও করেছেন। পারসি সুফি হাল্লাজ নিজেকেই বিধাতা (আনাল হক) বলেছেন। মানুষের চন্দ্রে গমনের ৫০ বছর পার হয়ে গেছে। অচিরেই মঙ্গল গ্রহে বসতি স্থাপন হবে। এক ফসলি জমি তিন ফসলি হয়েছে, ৭০০ কোটি লোকের অন্নের সংস্থান হয়েছে (যদিও খাদ্য বন্টন সর্বত্র মানবিক নয়!)। বিশেষজ্ঞরা দাবি করেন, পৃথিবীতে ১০০০ কোটি পর্যন্ত লোকসংখ্যার খাবারের ব্যবস্থা করা সম্ভব। এবং ততদিনে অন্যগ্রহে লোকজনের মাইগ্রেশন শুরু হয়ে যাবে। এক-দুইশ বছরের মধ্যে মানুষ কাজকর্ম ছেড়ে সব সময় অবসরে কাটাবে। এ গ্রহে সে গ্রহে বেড়াতে যাবে। কারন রোবোটরা তখন সব কিছু করবে। আমাদের কিছুই করার থাকবে না। ইচ্ছামত আয়ু বড়ানো যাবে। কিন্ত মত্যু কি ঠেকানো যাবে? বৈজ্ঞানিকরা এর উত্তর দিতে ইতস্তত করেন। এত শত বছরের পিরামিডও ইলেক্ট্রো ডায়ানিমিক থিয়োরির তিন নম্বর সূত্র অনুযায়ী একদিন ধ্বংস হবে। পৃথিবীও ধ্বংস হবে। এমনকি বিশ্বব্রহ্মান্ডও একদিন, হাজার কোটি বছর পরে হলেও, ধ্বংস হবে! তাহলে মানবজীবনের ভরসা কি?
তাই আপাতত ‘সময়-ভ্রমণের’ স্বাদ নেয়া যাক। অতীত বা ভবিষ্যতে যদি মানুষ একদিন ‘ওয়ার্ম (কীট) হোল, ব্লাক হোল বা হোয়াইট হোল’ দিয়ে যাতায়াত করতে পারে, মন্দ কি! মৃত দাদা-দাদি, নানা-নানি, বাবা-মা, বন্ধু, প্রিয়জনদের সাথে সাক্ষাত হবে। ভবিষ্যতের সাথেও অগ্রিম সাক্ষাত হবে। এ বইয়ের কাহিনীটি আমার মনঃচিকিৎসককে বিস্তারিত বলার পর, তার অভিমত ছিল, ‘ঘটনাটি অতীতের সাথে আমার সাক্ষাৎকার’! হবেও হয়ত। আমি নিশ্চিত নই। সত্য না অসত্য, তা নির্ধারণ করার দায়িত্ব পাঠক-পাঠিকাদের উপরে ছেড়ে দিলাম।
অবতরণিকা
শহরের উত্তর প্রান্তে পাশাপাশি দু’টি পনেরো তালার গগনচুম্বি অট্টালিকা। তেরো ও পনেরো নম্বর। ইউরোপে জোড় ও বেজোড় নম্বরের বাড়ি রাস্তার দুদিকে একসারিতে থাকে। সেজন্য এ দুটি বিল্ডিং পাশাপাশি, মাঝে কয়েকশ গজের ফারাক। এদের অনেকেই ‘যমজ বোন’ বলে থাকে। শহরে এরাই সর্বোচ্চ।
ত্রিশ বছর একটানা দক্ষিণ জার্মানির স্টুটগার্টের ববলিংগেন-এর প্রতিবেশী চারটি শহরে পর্যায়ক্রমে বসবাসের পর ২০০৬ সালে আমি এখানে এই শহরে চলে আসি। ফ্রাংকফুর্ট এয়ারপোর্টের দশ মাইল দুরে, নয়ে-ইজেনবুর্গ। একে এয়ারপোর্ট-শহরও বলে। পুব-পশ্চিমে আসা-যাওয়ার সময় উড়ন্ত প্লেনে যাত্রীরা এদের আকাশ থেকে দেখতে পায়। আমিও বহুবার দেখেছি। এখানের আকাশে বিমান টেক অফ করার সময় বা নামার সময় এমন নিচু হয়ে যায়, মাঝে মাঝে আমি আমার এগারো তলার ফ্ল্যাটের ব্যালকনি থেকে প্লেনের প্রচন্ড শব্দ শোনার সাথে সাথে গোল জানালা দিয়ে ভেতরের যাত্রীদের আবছা আবছা মাথার ছায়াও মনে হয় অনুভব করি।
এখন জুলাই মাস। ভর গ্রীষ্ম। সকাল চারটার মধ্যেই সূর্যোদয় এবং ২০-৩০ মিনিটের মধ্যেই পুরোপুরি দিন হয়ে যায়। সারারাতই গুমোট ভাব থাকে এবং কাকভোরেই সূর্যালোকের তীক্ষ্ণ খোঁচায় নিদ্রা পালিয়ে বাঁচে। সারা শরীরে পাঁচপ্যাচে ঘাম। তাপমাত্রা ত্রিশ ডিগ্রির দিকে ধাবিত। বাংলাদেশের কথা মনে হয়ে যায়। প্রতিবেশ-পরিবেশ-আবহাওয়া গত দু‘দশক ধরেই তালগোল পাকিয়ে যাচ্ছে।। জুন মাস থেকেইএখন ইলেক্ট্রিকের দোকানে নানা রকম ফ্যান ও কুলারের সমাবেশ- যা দশ বছর আগেও দেখতাম না। অনেকদিন সন্ধ্যার দিকে পানির সাপ্লাই ম্লান হয়ে যায়। এক গ্লাস পানি ভরতে কয়েক মিনিট লাগে।
আমি আজ ভোর চারটেয় উঠে কাঁধের ব্যাগ গুছিয়ে এক কাপ কফি ও দু’টি শুকনো টোস্ট রুটি কোনোমতে চিবিয়ে, হাফ প্যান্ট ও স্যান্ডো গেঞ্জি গায়ে দিয়ে বেরিয়ে পড়েছি। গন্তব্য চৌদ্দ কিলোমিটার দূরে বিটবুর্গের চারটি গ্রামে যা এখনও অবশিষ্ট আছে, এবং যে কয়েকজন এখনও ওখানে বাস করছেন, তাদের সাথে, বলতে গেলে, শেষ দেখা করতে। চারটি গ্রামের নম্বর দিয়ে নাম। বিটবুর্গ-১ থেকে ৪। আমি যখন ২০০৬ সালে এখানে আসি, সব গ্রাম মিলিয়ে লোক সংখ্যা ছিল তিনশ‘র মত। সবই কৃষক পরিবার। তার মধ্যে কয়েকজন গৃহসংলগ্ন খেতে ট্রাক্টর দিয়ে গম চাষ করত। এক নম্বর গ্রামে ছিল দু’টি পরিবার। একটি বাড়িতে মধ্যবয়স্ক মেলি একা থাকতেন। গত শতাব্দি পর্যন্ত এখানে মধ্যযুগীয় গ্রামাঞ্চলের বৈশিষ্ট্যপূর্ণ ও নয়নাভিরাম সব কৃষকের বাড়ি দেখা যেত। তিন তলা, কাঠের তৈরি। ছাদ টালির। নিচের তলায় গোয়াল ঘর, দোতালায় বসার ঘর, রান্না ঘর, স্টোর ও পড়ার ঘর। তিন তলায় ২-৩টে (প্রয়োজন মাফিক) শোবার ঘর। সামনে পেছনে প্রায় একবিঘার মত বাগান। নানারকম ফুল ছাড়াও বিভিন্ন ধরনের ঋতুকালীন তরকারির চাষ করত পরিবারের সবাই মিলে। এক সময় বলা হত. লবন-চিনি ছাড়া তাদের বাইরে থেকে কিছুই কিনতে হতো না। খেতের গম, রাই থেকে ভেষজ তেল, বাড়ির বাগানের শাকসবজি। দুধ বন্ধ হয়ে গেলে গরু তার শেষ কর্তব্য পালন করত গায়ের মাংস আহার হিসেবে প্রদান করে। হাঁস-মুরগী তো ছিলই। বয়সের প্রভাবে ডিম-প্রসব বন্ধ হয়ে গেলে চিকেন-স্যুপ ও রোস্টের ব্যবস্থাও হতো। এক সময় পাশেই একটি ছোট নদী ছিল (এখন শুকিয়ে গেছে), সেখানে মাছ ধরা হতো। কয়েকটি জলাশয়ও ছিল। ধীরে ধীরে সেগুলি বুঁজিয়ে ফেলা হয় নতুন রাস্তাঘাট, বাসভবন, স্কুলঘর ইত্যাদি বানানোর জন্য। সভ্যতার প্রসারণ! এ ধরনের স্বয়ংসম্পূর্ণ গ্রাম নাকি এক সময় (২-৩ শ বছর আগে) আমাদের দেশেও ছিল। বইপুস্তকে পড়েছি।
আমি প্রথম যখন টাটকা শাকসবজি ও দুধ কেনার জন্য বিটবুর্গে আসি, তখন বাড়িঘরের প্যাটার্ণ আগের মতই ছিল। কিন্ত প্রথম তলায় গোয়াল ঘর উঠে গিয়ে গাড়ি ও ট্রাক্টর রাখার গ্যারেজ হয়ে গিয়েছিল। বিটবুর্গ-১ এ মিসেন মেলি সালফেল্ড একাই থাকতেন। তিনটি দুধের গরু, বাড়ির সামনে পেছনে শাকসবজির চাষ করত।। একাই সবকিছু করত। বছর দশেক আগে স্বামীর মৃত্যু হয়েছিলো। তার কাছে বহুবার স্বামী আলেক্সের দীর্ঘদিন ক্যান্সারে ভূগে, আমানষিক কষ্টভোগের করুণ কাহিনী শুনছি। স্বামীর স্মৃতি দশ বছরেও বিন্দুমাত্র ম্লান হয়নি। একমাত্র মেয়ে রেবেকো বিয়ের পর স্বামীর সাথে বহু আগে থেকেই আমেরিকা প্রবাসি। ২-৩ বছরে একবার আসে মাকে দেখতে। মেলির এখনও সংসারের কাজকাম ফেলে আমেরিকা যাবার সুযোগ হয়নি। একটা হাফ ট্রাক চিল। ওটা দিয়ে তরকারি, বোতলে দুধ ভরে, গৃহপালিত হাঁস-মুরগীর ডিম, আশেপাশের শহরের সাপ্তাহিক হাটে হাটে ফেরি করতো। ট্রাকটির পেছনে এক দিকের পার্টিসন ফেলে দিয়ে লম্বা টেবিলে রাখা শাকসবজি-দুধের বোতল, ডিম, ক্রেতাদের নিজেদের হাতেই নিতে হতো। মেলি দাঁড়িপাল্লার কাজ আর দাম বুঝে নিতো। এ শহরের সাপ্তাহিক বাজারেই আমার সাথে তার পরিচয় হয়েছিল। আমি তখন দোকান থেকে খাবার জিনিস পারতপক্ষে কিনতাম না। এখনকার কথা অবশ্য আলাদা। অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে অভ্যাসের কত পরিবর্তন হয়েছে! পরে শনিবারের প্রতিক্ষায় না থেকে মাঝে মাঝে সাইকেলে মেলির বাড়ি গিয়ে কেনাকাটা করতাম। একা থাকে। আমি গেলে (আরও কেউ কেউ একই উদ্দেশ্যে যেত) ও খুব খুশী হতো। না খাইয়ে ছাড়ত না। বুঝতাম জীবিকার জন্য সে এইসব হাটে সওদা নিয়ে যায় না। নিজেও বহুদিন চাকরি করেছেন। ভাল পেনশন পেতেন। মৃত স্বামীর (চাষবাস ছাড়াও তার ইলেকট্রিকের দোকান ছিল) সঞ্চয় ও তার পেনশনের যে অংশ সে পেত, তার এসব করার কোনই দরকার ছিলনা। কিন্ত ইউরাপের প্রচন্ড সমৃদ্ধির নিচেই ছিল একাকিত্বের সর্বগ্রাসী অন্ধকার। দু’টি মহাযুদ্ধের জেরে জার্মানিতে পুরুষ-মহিলার সমানুপাত ছিল না। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধর পর নিঃসঙ্গ মহিলাদের সর্বস্তরে কাজ করতে হয়েছে- যা এক সময় পুরুষ করেছে। সত্তর দশকে জার্মানিতে এসে আমি মেলির মত বহু একলা মহিলার সাথে পরিচিত হয়েছিলাম, যারা কয়েক দন্ড কারো সাথে কথা বলতে পারলে, মহা সুখ অনুভব করত।
সেজন্য মেলির সাথে আমার একটা ভালো সম্পর্ক হয়ে গিয়েছিল। হিসেব করলে বয়সে সে আমার বেশ বড়, আমার তখন ষাটের কাছাকাছি, ওর ৭২! কিন্ত একটা শিশুর মত মিশুক মন, সাদাকালোর কোন প্রশ্ন তার মধ্যে ছিল না। গীর্জায় যেত নিয়মিত। তবে ধর্মান্ধ ছিল না। খুব একটা মাখামাখি আমাদের কখনই হয়নি। কিন্ত মাসে ২-৩ বার দেখা হতো। সেও শহরে এলে কিছু না কিছু আমার জন্য নিয়ে আসত। দুধ, টমেটো, আলু, ডিম এসব। বাসায় আমাকে না পেলে ঘরের সামনে রেখে যেত। আমি বহুদিন বাইরে থেকে বাসায় ফিরে এসে এরকম অপ্রত্যাশিত টাটকা খাবার দেখে খুবই আনন্দ পেয়েছি। ক্রিসমাস, ইস্টারের উৎসবের সময় আমি ছিলাম তার নিয়মিত অতিথি। আমি অনেক সময় হাসপাতালে থেকেছি। মেলি একবার দু’বার আমাকে দেখতে যেত।
বিটবুর্গের চারটি গ্রাম বিশ্বায়নের শিকার! কাছেই ৭-৮ কিলোমিটার দূরে গত শতাব্দির নব্বই দশকে তাউনুস পাহাড়ি এলাকায় পাথরের একটা বিশাল খনি আবিস্কৃত হয়েছিল। কয়েকশ কোটি বর্গমিটার! রাস্তা ও বাড়িঘর নির্মাণে পাথরের ব্যবহার আমরা সবাই জানি। কিন্ত এর সবচাইতে লাভজনক দিকটি হল সিমেন্ট তৈরি। সিমেন্ট বর্তমান যুগে সব কিছু নির্মাণে একটি আবশ্যিক উপাদান। প্রাদেশিক সরকার গবেষণা দল নিয়োগ করলেন। তাদের পেশ করা ২০০৫ সালের প্রতিবেদনে জানা গেল তাউনুস এলাকার পাথরের রিজার্ভে একটানা একশ বছর সিমেন্ট উৎপাদন করে জার্মানির গোটা প্রয়োজনের শতকরা ত্রিশ ভাগ মেটানো যাবে। কোটিপতি ব্যবসায়ী ও বিল্ডারদের ঘুম হারাম হয়ে গেল। ঘরের কোনায় এত বড় টাকার গাছ! সরকারের খাজনা প্রাপ্তির যে হিসাব করা হল, তাতে জনসাধারনের মুখ দিয়েও লালা পড়া শুরু হল। শুধু সিমেন্ট কারখানাই নয়; বৃহৎ একটি কাগজের মিল, মটর গাড়ির পার্টসের কারখানা এবং লাস্ট নট দি লিস্ট- এদের সঙ্গে একটি কম্পিউটার-শহর তথা সিলিকন ভ্যালির একটি কনিষ্ঠ ভ্রাতারও জন্ম দেয়া সম্ভব। সব মিলিয়ে পঞ্চাশ হাজারের উপরে নতুন চাকরি, তাদের বসবাসের জন্য বহুতল বিশিষ্ট ফ্ল্যাটবাড়ি, ছেলেমেয়েদের জন্য স্কুল-কলেজ ইত্যাদি। আমোদ প্রমোদ, বিনোদন, রেস্টুরেন্ট এবং হোটেল। যেদিতে তাকাও শুধু চাকরি, বিলাস, বৈভব, অর্থের পাহাড়। আনুমানিক তিনহাজার কোটি ইউরো বিনিয়োগ হবে- যা প্রথম তিন বছরেই উঠে আসবে। তারপর শুধু ক্যালকুটার দিয়ে টাকা গোনা, স্রোত হবে একমুখি, ব্যয় কম, আয় বেশি। সিমেন্ট বানাও, কাগজ বানাও, পার্টস বানাও, কম্পিউটার বিক্রি, আর কি চাই। চার গ্রামের তিনশ‘ লোকের ৫০-৬০টি পরিবারের প্রতিবাদ, আপত্তি, আহাজারি কে শোনে? সাত-আটশ বছরের একটি প্রাচীন জনপদের মৃত্যুদন্ডের রায় চুড়ান্ত হয়ে গেল। কাছের অফেনবুর্গ শহরে সবার নতুন বাড়ি (ফ্র্রি) দেয়া হবে, নগদ ক্ষতিপূরণও দেয়া হবে। যার যার পছন্দমাফিক বাড়ি তৈরি করে দেবে সরকার। যতদিন পুনর্বাসন শেষ না হচ্ছে, পরিবারের ছেলেমেয়েদের সরকারি বাসে ঐ শহরের স্কুলে বিনামূল্যে যাতায়াতের ব্যবস্থাও করা হবে। সবচাইতে মোক্ষম টোপ- নতুন প্রকান্ড শিল্প এলাকায় সব প্রতিষ্ঠানে চাকরি পাওয়ার অগ্রাধিকার থাকবে উচ্ছেদ-পরিবারের সন্তানদের। যোগ্যতার প্রশ্নও প্রয়োজন হলে শিথিল করা হবে! জার্মানিতে ভালো একটা স্থায়ী চাকরি হল এ জীবনের সবচাইতে বড় প্রাপ্তি। কাজেই যেসব পরিবার প্রতিবাদ করছিল, উচ্ছেদের বিরুদ্ধে কোর্টে কেস করেছিল, শহরে এসে নিয়মিত প্রসেশন করত, ‘প্রাণ গেলেও বাড়ি ভাঙ্গতে দেব না’ বলে অনশন-অবস্থান ধর্মঘট করত, তারা একে একে তাদের পিটিশন প্রত্যাহার করে নিল। ঐতিহ্য-সংস্কৃতি, পিতৃপুরুষের ভিটার জন্য টান-ইতিহাস সব চুলোয় গেল বিনামুল্যে নতুন বাড়ি আর সন্তানদের চাকরির নিশ্চয়তা এবং নগদ টাকার বন্যায়! এ এলাকা থেকে যে মোট বিশ হাজার একরের জঙ্গল কেটে ফেলা হবে, কাগজের মিলের জন্য প্রতি বছর একটা ছোটখাট শহরের সমান বনভূমি বিরান করা হবে, এগুলি আর কারো মনে রইল না। গত চল্লিশ বছরে জার্মানিতে এধরনের দ্বিমুখী আচরন (মোনাফেকি বলা যায়) আমি বহুবার দেখেছি। উদ্ভিদ-জঙ্গল-বন-প্রেম, ‘প্রতিবেশ রক্ষার জন্য প্রয়োজন হলে প্রাণ বিসর্জন দেব’ এই সব স্লোগান নিমিষেই মিলিয়ে যেতে দেখেছি, যখন ব্যক্তি ও গোষ্ঠিস্বার্থ উঠে এসেছে।
এসব করুণ ও দুঃখের অনেক কাহিনী বিটবুর্গে গেলেই শুনতাম। বিশেষ করে বয়স্ক, বৃদ্ধরা তাদের ভিটামাটির জন্য শোক করতেন। মেলি তো বলতে বলতে কেঁদেই ফেলতো। ও ওর বাড়িটিকে ভীষণ ভালোবাসত। সে এবং আরও ১০-১২ জন ২০১০ সনেও সরকারি উচ্ছেদ পরিকল্পনায় সায় দেয়নি। তার একমাত্র প্রতিবেশী নিঃসঙ্গ মহিলাটি অফেনবুর্গে একটি বৃদ্ধাশ্রমে ২০০৮ সালে চলে গিয়েছিল। মেলি বলেছিল, ও প্রায় এক লাখ ইউরো ক্ষতিপূরণ পেয়েছে। তাই দুই ছেলে সপরিবারে এসে মাকে দিনরাত চাপ দিয়ে উচ্ছেদের সম্মতি আদায় করে ভাগের টাকা নিয়ে যার যার শহরে চলে গেছে। এখন মাকে দেখতে একবারও আসে না। গরুর দুধ দেয়া বন্ধ করলে যেমন কসাইয়ের কাছে বেঁচে দেয়া হয়, সন্তানরা সে নীতিই গ্রহণ করেছে। মায়ের তো আর এখন কিছুই অবশিষ্ট নেই। তারপর থেকে মেলি একাই এক নম্বর গ্রামটিতে থাকত। ওকে দেখলে আমার ‘কালের সাক্ষী বটবৃক্ষ’ মনে হত!
বিটবুর্গ-২ এ ছিল সেন্ট অগাস্টিন গীর্জা। সাতশ বছরের পুরানো। ১২৮৭ সালে স্থানীয় এক নিঃসন্তান রাজা সন্তান প্রাপ্তির জন্য এ গীর্জাটি নির্মাণ করেছিলেন। তারপর থেকে এখানে নিরন্তর নিঃসন্তান দম্পতিদের আনাগোনা। এই এলাকার একটি মাত্র আবাসিক হোটেল চার নম্বর গ্রামে। বাইরে থেকে আগত দম্পতিরা সন্তান কামনায় এই গীর্জায় প্রার্থনা করতে আসতেন। গীর্জার ভালো রোজগার হত, হোটেলের মালিক খুশি। এ এলাকার একটিমাত্র রেস্টুরেন্টও ছিল চার নম্বর গ্রামে। গীর্জার দর্শনার্থীরাই ছিল প্রধান খদ্দের। হোটেল ও রেস্টুরেন্ট একসাথে ২০০৯ সালে উঠে যায়। চার নম্বর গ্রামেই এক সময়ে ২৫-৩০টি পরিবার থাকত। সংখ্যার হিসেবে এখানেই ছিল সবচাইতে বেশি লোক। সবাই ঐ বছরই বাড়ীঘর ছেড়ে দিয়ে অফেনবুর্গে যার যার নতুন বাড়িতে চলে যায়। ২০১০ সাল পর্যন্ত দুই ও তিন নম্বর নম্বর গ্রামে মোট বারোটি পরিবার ছিল। এখন আর কেউ নেই।
দুই নম্বর গ্রামে শুধুমাত্র একটি জেদী বৃদ্ধ দম্পতি এখনও রয়েছে। বরাবর নিঃসন্তান। কিন্ত বাপের ভিটার অন্ধ ভক্ত। কর্র্তৃপক্ষ শতবার বৈঠক করেও ওদের এখনও বাড়ি ছাড়া করতে পারেননি। বহু লোভনীয় প্রস্তাব এই বৃদ্ধ দম্পতি নিঃসংকোচে প্রত্যাখ্যান করে চলেছে। এই গ্রামেই গীর্জার পাদ্রি জন এখনও আছে। তিনিও মার্টিন ও শার্লটকে (বৃদ্ধ দম্পতি) বহু বলেও ভিটা ছাড়তে রাজী করাতে পারেনি। ওর সাথে আমার প্রথম থেকেই সখ্যতা। বয়স আমার অর্ধেক। তবে খুবই শিক্ষিত, উদার এবং মানবিক গুনসম্পন্ন। চারপুরুষ ধরে তারা গীর্জার পাদ্রি। মাও এক সময় একটি গীর্জায় পুরোহিতের কাজ করেছেন। জনরা প্রটেস্টান। সেজন্যই এদের বিয়ের অনুমতি আছে, মেয়েরা ধর্মানুষ্ঠান পরিচালনা করতে পারে। ক্যাথলিক-পাদ্রিদের চাকরির প্রধান শর্তই হল, কৌমার্য। বিবাহ করতে পারে না। সাধারণের জন্য বিবাহ-বিচ্ছেদও নিষিদ্ধ। মেয়েরা গীর্জায় আসতে পারে কিন্ত বেদীতে উঠতে পারে না! জার্মানরা ধর্মের ব্যাপারে রক্ষণশীল নয়। কিন্ত মুলতঃ ধার্মিক। বিশেষ করে শহরের বাইরে যারা গ্রামে থাকে তারা ধর্মের প্রতি বেশ অনুরাগী। বয়স্ক ও বৃদ্ধরা মৃত্যুর সন্ন্কিট বলেই হয়ত (সুস্থ থাকলে) নিয়মিত রবিবারে গীর্জায় যায়। বিটবুর্গের ধর্মীয় সমাজ ঐতিহ্যবাহী এই গীর্জাটির রক্ষায় ঐক্যবদ্ধ হয়ে দেন দরবার শুরু করল। জন নেতুত্ব দিয়েছিল। জার্মানিতে বহু গীর্জার উচ্ছেদ হয়েছে। এলাকায় কয়লার খনি আবিস্কৃত হয়েছে, বা নদীর স্রোত ঘুরিয়ে বিদ্যুতের ব্যবস্থা করতে হয়েছে। এসব কারণে অনেক গীর্জাই এখন আর নেই। তবে কয়েকটি গীর্জা ঐতিহাসিক মুল্যের কারণে বা প্রত্নতাত্তিক প্রেক্ষাপটে স্থানান্তরিত হয়েছে। প্রচুর খরচ হয়, দীর্ঘ সময় লাগে। তবে জার্মানির সমৃদ্ধি এবং ধার্মিক ব্যক্তিদের লক্ষ লক্ষ টাকার চাঁদায় এধরনের ব্যয়বহুল প্রকল্প এখানে সম্ভব। বিটবুর্গের গীর্জার রক্ষার জন্য স্থানীয় ছাড়াও জাতীয় ও আন্তর্জাতিক চাপও ছিল। এ এলাকা থেকে শত বছর আগে চলে যাওয়া আমেরিকা-কানাডার অর্থবান অভিবাসিরাও এজন্য কয়েক লাখ ইউরো চাঁদা দিয়েছেন। মোট সাত মিলিয়ন বাজেটে গীর্জাটিকে অফেনবুর্গে (পনেরো কিলোমিটার দুরে) সরিয়ে নেবার পরিকল্পনা চুড়ান্ত হয়েছে। আগামী নভেম্বর মাস থেকে কাজ শুরু হবে। দেড়-দু‘মাসে গীর্জাটি নিচের তলার বেসমেন্টসহ নতুন জায়গায় বাসাবদল করবে। এই জায়গা বদলের জন্য বিশেষভাবে নির্মিত একটি প্রশস্ত ট্রেনে (এজন্য লাইন বসানো হচ্ছে) গীর্জাটি প্রতিদিন দশঘন্টা করে মাত্র ৩০০ মিটার করে গন্তব্যের দিকে অগ্রসর হবে। পরে এ প্রসঙ্গে আবার বিশদ আলোচনা করব। (চলবে)
নয়ে-ইজেনবুর্গ, জার্মানি ২০ ডিসেম্বর, ২০২১